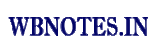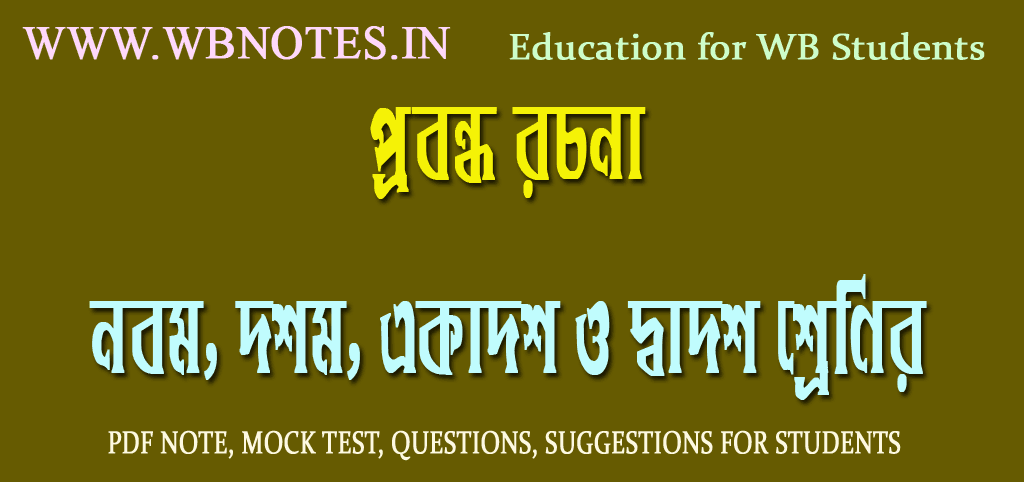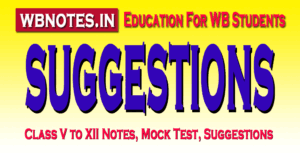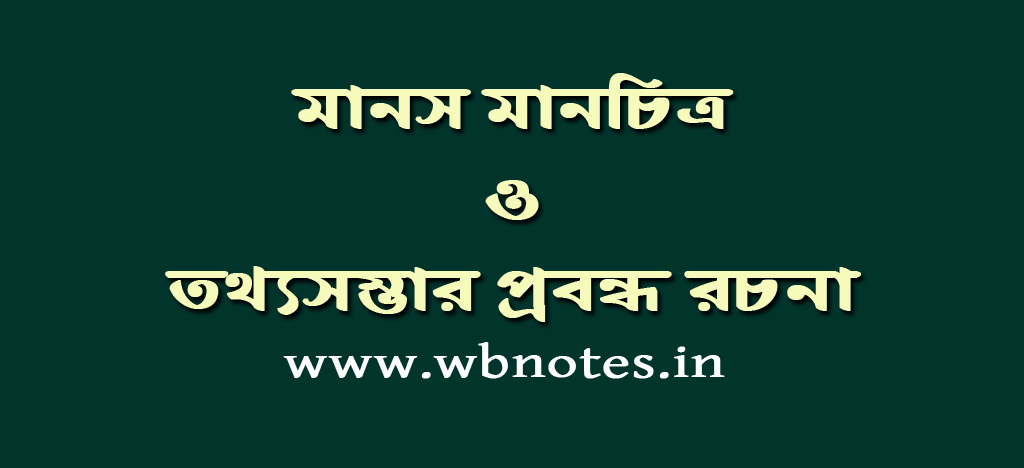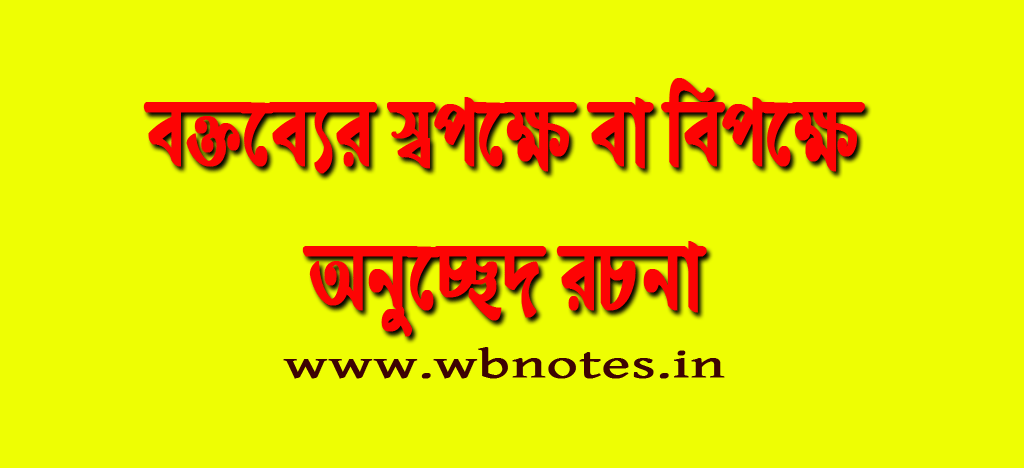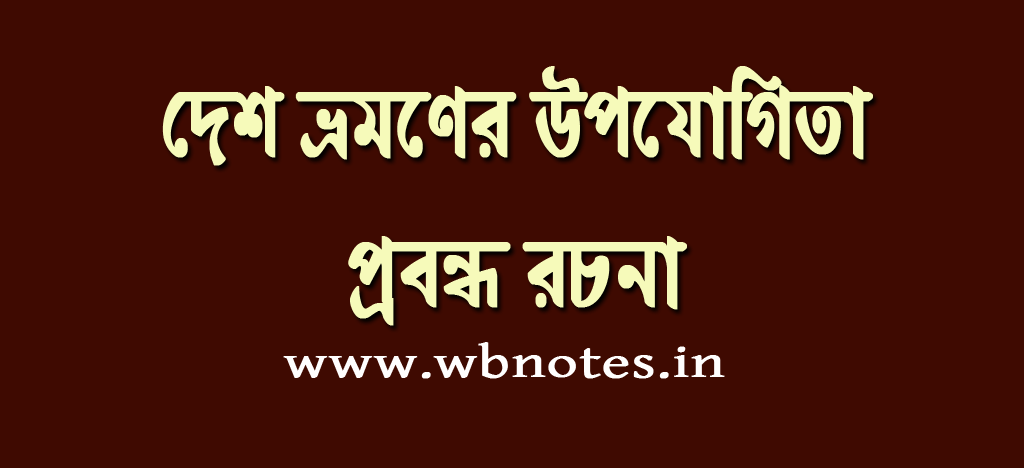প্রবন্ধ রচনা
আমাদের WBNOTES.IN ওয়েবসাইটের পক্ষ থেকে এখানে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবন্ধ রচনা প্রদান করা হলো। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীর অনুচ্ছেদ রচনা তোমাদের নির্দিষ্ট শ্রেণির নোট বিভাগে ইতিপূর্বেই প্রদান করা হয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই রচনাগুলি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তোমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা তথা মাধ্যমিক, একাদশ দ্বিতীয় সেমিস্টার ও দ্বাদশ চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে।
প্রবন্ধ রচনা :
সমাজের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য
ভূমিকাঃ
সমাজ একটা সংঘবদ্ধ ব্যবস্থা, মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্ষেত্রভূমি। সমাজের মধ্য দিয়েই মানুষ তার পাশব প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে মনুষ্যত্ব অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ‘মানুষ জন্মায় ভূমিকা জন্তু হয়ে, কিন্তু এই সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।’ কাজেই যে-সংঘবদ্ধ ব্যবস্থা বা সমাজ মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে, তাকে অবশ্যই ক্লেদমুক্ত রাখা দরকার, সুন্দর করে গড়ে তোলা দরকার। আর এ কাজে প্রতিটি সামাজিক মানুষের কিছু না কিছু কর্তব্য থাকে। ছাত্রছাত্রীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। অধ্যয়ন ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লক্ষ্য, একথা মেনে নিয়েও বলা যায়, অধ্যয়নের পাশাপাশি সমাজের প্রতিও তাদের অনেক কর্তব্য আছে।
নিরক্ষরতা দূরীকরণেঃ
আমাদের দেশে সার্বিক শিক্ষার হাল অত্যন্ত খারাপ। এখানে নিরক্ষরতা এখনও একটি সামাজিক অভিশাপের মতো। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে কেবল সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। ছাত্রসমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজেদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষর করে তোলার কাজে খুব সহজেই উদ্যোগী হতে পারে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে যোগ দিয়ে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা সাক্ষরতা প্রসারে সচেষ্ট হলে বহু নিরক্ষর মানুষকে অল্পদিনের মধ্যেই সাক্ষর করে তোলা সম্ভব। দায়ীদে
স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায়ঃ
সাক্ষরতা প্রসারের মতো স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য-সচেতনতার বড় অভাব। গ্রাম ও শহরের বহু অঞ্চলে পরিবেশ এতই অপরিচ্ছন্ন যে, সেইসব জায়গা থেকেই নানা রোগের জীবাণু ছড়ায়। এই অপরিচ্ছন্নতার প্রতিকারের জন্য ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই হাত লাগাতে পারে। নালা-নর্দমা পরিষ্কার, আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে এলে গ্রামে শহরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস লক্ষ করা যায়। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই কেউ কেউ সর্বনাশা ড্রাগের নেশায় আজ আচ্ছন্ন। তাদেরকে এই পতনের হাত থেকে উদ্ধার করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও নিতে হবে ছাত্রসমাজকে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের যে চেষ্টা চলছে তাতে অতি অবশ্যই ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত।
ত্রাণকার্যেঃ
বন্যা, ভূমিকম্প, খরা, অগ্নিকাণ্ড, বড় কোনো দুর্ঘটনা প্রভৃতিতে মানুষ বড় অসহায় হয়ে পড়ে। এইসব ক্ষেত্রে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে ছাত্রসমাজ। উদ্ধারকার্যে এবং ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা উদ্যোগী হলে অনেক অসাধ্যসাধন হতে পারে। দুর্গত মানুষের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ছাত্রসমাজ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা ছাড়াও অনেক সময় অনেক মানুষের জীবনে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে। ছাত্রছাত্রীরা যদি সেইসব দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই খুবই উপকৃত হবে।
প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়েঃ
আমাদের সমাজ এখনও পদে পদে নানান কুসংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ। এর কারণ অজ্ঞতা এবং প্রথার প্রতি নির্বিচার আনুগত্য। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও প্রথা ও কুসংস্কারের প্রভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বল মানসিকতার সুযোগেই সমাজে আজও নানান তুকতাক, তাবিজ-মাদুলি আর পরশুরামের ‘বিরিঞ্চিবাবা’র মতো ভণ্ড সাধুদের রমরমা। ছাত্রসমাজকে এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের মন থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে কুসংস্কারকে। পণপ্রথার মতো একটি সামাজিক পাপকে বিনাশ করার ক্ষেত্রেও ছাত্রসমাজের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তারা নিজেরা যদি ছাত্রজীবন থেকে সংকল্প করে যে, এই প্রথাকে তারা কখনো প্রশ্রয় দেবে না, তাহলে ধীরে ধীরে সমাজ থেকে এই প্রথার অবলোপ অসম্ভব নয়।
প্রতিবাদে ও জাতীয় সংহতি রক্ষায়ঃ
সমাজে প্রতিনিয়ত কত যে অন্যায়-অবিচার ঘটে চলেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এইসব ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কখনো কখনো বিদ্বেষ-বিষ প্রবল হয়ে ওঠে। দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। সংকীর্ণ এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে যে আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, জাতীয় সংহতি বিধানের পক্ষে তা খুবই অনুকূল। কাজেই তারা সমাজের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা জাতীয় সংহতি রক্ষার পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে।
উপসংহারঃ
ছাত্রশক্তি সমাজের একটা বৃহৎ শক্তি। এই শক্তি যদি বিভিন্নভাবে সমাজের কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হয়, তাহলে সমাজের রূপ যে অনেকটাই বদলে যাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের কেবল ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির কথা ভাবলে চলবে না, ভাবতে হবে সমাজের কথাও। মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে হলে চাই আদর্শ সমাজ। ছাত্রছাত্রীরা সচেষ্ট হলে একদিন না একদিন সেই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবেই।
ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য
ভূমিকাঃ
“আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল
আমরা ছাত্রদল।”
-কাজী নজরুল ইসলাম
ছাত্ররাই একটি দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের দিকেই তাকিয়ে থাকে দেশ ও সমাজ। তারা ভোরের শিশির, প্রভাতের আলোর মতো নবজীবনের দ্যুতি ছড়ায়। তারা তাদের কর্মে দেশ ও সমাজের সব অনাচার, অবিচার, অসঙ্গতি দূরে ঠেলে দেয়। তাদের মধ্যে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। তারা পারে না এমন কাজ পৃথিবীতে নেই। ছাত্রসমাজ জেগে উঠলে পুরো জাতি, দেশ ও পৃথিবী জেগে উঠে। তারা তাদের সংগ্রাম দিয়ে যেমন দেশকে সংঘাত মুক্ত করে তোলে, তেমনি নৈতিকতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যতা দিয়ে দেশকে সুখী ও সুন্দর করে তোলে।
ছাত্রজীবনঃ
অধ্যায়নের জীবনটাই ছাত্রজীবন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে দেশের বাইরে বিভিন্ন গবষেণামূলক অধ্যয়নের সবটুকুই ছাত্রজীবনের অন্তর্ভুক্ত। একজন ছাত্র কোনো কিছুতেই পিছপা হয় না। ছাত্রজীবন মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ছাত্রজীবনেই মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত গড়ে তোলে। জীবনকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে তোলার শিক্ষা মানুষ ছাত্রজীবন থেকে পায়। বদান্যতা, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, মহানুভবতার শুরু ছাত্র জীবন থেকেই। প্রতিটি ছাত্রই দেশগড়ার হাতিয়ার। ভবিষ্যতে তারাই দেশের নেতৃত্ব দিবে। M.K Gandhi বলেছেন- “The students are the Future leaders of the country who could fulfil country’s hopes being capable.”
ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ
“ছাত্র নং অধ্যয়নং তপ”
-এটিই ছাত্রদের মূলমন্ত্র। সংস্কৃত এই কথাটির অর্থ- অধ্যয়নেই ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা। ছাত্রজীবন মানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ। যেখান থেকে ছাত্ররা প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শিখবে। আর এ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে কর্মমুখী জীবনে প্রবেশ করবে। স্বাস্থ্যকর, মানসম্পন্ন, সুন্দর পরিবেশে কাজ করতে চাইলে ছাত্রজীবন থেকেই সেই মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রজীবনে পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। তার পাশাপাশি মানুষ্যত্ববোধও অর্জন করতে হবে। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। শিক্ষকের আদেশ পালন করলে একটি ছাত্র অবশ্যই ভালো গুণের অধিকারী হতে পারবে। কেননা শিক্ষকই একটি ছাত্রকে সৎ ও মেধাবী করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “None but those who have the spirit of forbearance are fit to be teacher.”
তাই শিক্ষককে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করতে হবে। ছাত্রদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ না থাকা। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক কিছু শেখার রয়েছে যা তাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে।
সামাজিক ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ
একটি দেশের সচেতন নাগরিক হচ্ছে ছাত্রসমাজ। অধ্যয়ন ছাত্রদের মূল লক্ষ্য হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তারাই দেশকে সঠিক পথ অনুসরণে সহায়তা করতে পারে। আমাদের দেশে এমন অনেক দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত পরিবার রয়েছে যেখানে একটি মাত্র সদস্য শিক্ষিত। সেই সদস্যটি পুরো পরিবারে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। শুধু পরিবার কিংবা সমাজ নয় ছাত্রসমাজকে পুরো জাতির নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মারাত্মক আকার ধারণ করছে সেসব দেশের ছাত্রসমাজের উচিত সংঘবদ্ধভাবে জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এবং অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সমাজকে এবং শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দায়িত্ব ছাত্রদেরই কাঁধে নিতে হবে। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর কারণে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব হয় না ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ছাত্রসমাজের উচিত নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা। শিক্ষিত যুবকরা যদি কৃষি কাজ, মৎস্য চাষ, পশুপালন, নার্সারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগায় তাহলে দেশের উন্নয়ন যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি বেকারত্বও হ্রাস পাবে।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ
ছাত্রসমাজ অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার। আদর্শগতভাবেই তারা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতির বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করা ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যুগে যুগে ছাত্রসমাজ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এবং স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। শিক্ষিত, ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন ছাত্রসমাজ কখনো পরাধীনতার গ্লানি বয়ে বেড়াতে চায় না।
তবে বর্তমানে ছাত্ররা রাজনীতির প্রকৃত আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাজি, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন দুষ্কৃতিমূলক কাজে জড়িয়ে নিজেদের মেধাকে নষ্ট করে ফেলছে।
পারিবারিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ
“Charity begins at home”
ছাত্ররা পরিবারের কাছ থেকে যেমন অনেক কিছু পায় তেমনি পরিবারের প্রতিও তাদের অনেক দায়িত্ব থাকে। পরিবারের সকলেই তাদের কাছ থেকে ভালো আচার ব্যবহার প্রত্যাশা করে। আব্বু-আম্মু এবং পরিবারের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, ছোটদের প্রতি স্নেহ করা তাদের কর্তব্য।
দেশাত্মবোধঃ
ছাত্ররা দেশপ্রেমকে তাদের অন্তরে লালিত করে। তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত বাজি রাখতে পারে দ্বিধাহীনভাবে। ছাত্রদের দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকায় তারা দেশকে আরও বেশি আপন করে নিতে পারে। ছাত্রসমাজ মানেই তরুণ সমাজ। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এই তরুণসমাজকে দেশের ও দেশের মানুষের সেবায় মগ্ন থাকতে হবে। তাদের মধ্যে কোনো ক্লান্তি, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। বন্যা-দুর্গত, ঝড়ে কবলিত এলাকায়, দুঃস্থ মানুষের পাশে সবসময় তাদের সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।
নিয়মানুবর্তিতাঃ
“Work while you work, play while you play, And that is the way to be happy.”
-এই নীতি মেনে চললে ছাত্ররা তাদের সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করতে পারবে। ছাত্রদের প্রথম কাজ পড়াশোনা। কখনোই তাদের একদিনের কাজ অন্যদিনের জন্য রেখে দিলে চলবে না। ব্যক্তিজীবনে, সমাজ জীবনে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছাত্রদের অবশ্যই নিয়মানুবর্তিতার সাথে সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। ছাত্রজীবন থেকেই নিয়মানুবর্তিতায় বেড়ে উঠলে কর্মজীবনও এর প্রভাব পড়বে।
নৈতিক মূল্যবোধ ও শিষ্টাচারঃ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের শুধু পরীক্ষা পাসের শিক্ষাই দেওয়া হয় না। তাদেরকে নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিষ্টাচারের শিক্ষা দেয়া হয়। নৈতিক মূল্যবোধ ছাত্রকে সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী সর্বোপরি সুন্দর চরিত্রের অধিকারী করে তোলে। প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য চাই নৈতিকতা। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ ছাত্রসমাজকে নম্র-ভদ্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী করে। পরিবারের সকলের প্রতি, শিক্ষকদের প্রতি, সহপাঠীদের প্রতি মার্জিত আচরণে ছাত্ররা সকলের কাছ থেকে ভালোবাসা, দোয়া এবং সাহায্য-সহযোগিতা পায়। নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধসম্পন্ন ছাত্রসমাজই পারে ভবিষ্যতে জাতির সুষ্ঠু নেতৃত্ব দিতে। তাই ছাত্রদের শিষ্টাচার ও নৈতিক মূল্যবোধের গুণে অর্জন করতে হবে।
উপসংহারঃ
দেশ ও জাতি সৎ, চরিত্রবান, নিয়মনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, সৌজন্যবোধসম্পন্ন পরিশ্রমী ছাত্রসমাজের কামনা করে। সাম্প্রতিককালে ছাত্রসমাজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন ধরণের অপরাধমূলক কাজ করছে। ছাত্র-রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। যা দেশ ও জাতির কাছে মোটেও কাম্য নয়। এভাবে চলতে থাকলে জাতি শেকড়হীন হয়ে পড়বে। তাই ছাত্রসমাজের উচিত তাদের প্রকৃত আদর্শে আলোকিত হওয়া। যে শিক্ষা ও মূল্যবোধ ছাত্ররা অর্জন করে ভবিষ্যতে তা পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগানো, ছাত্রদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।
শিক্ষাবিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা
“কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।”
ভূমিকাঃ
সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের ব্যাবহারিক জীবনেও ঘটে চলেছে নানা ধরনের পরিবর্তন। শিক্ষা পদ্ধতিতে যুক্তি নতুন নতুন প্রয়োগ কৌশল। অতীতে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল গ্রন্থ ও গুরুকৃত উপদেশ নির্দেশাবলী। এই মাধ্যমে মানুষ আমোদ প্রমোদ ও চিত্র বিনোদনের সুযোগ পেয়েছে অন্য দিকে এগুলির মাধ্যমে নীতিবোধ, বিবেকবোধ ইত্যাদি পরোক্ষ শিক্ষাও লাভ করেছে। কিন্তু এই সমস্ত উপায়ে সুপরিকল্পিত ভাবে গণ শিক্ষার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। বর্তমান যুগে বিশ্ব বিজ্ঞানের অনন্য বিজয়ের ফলে সংবাদ পত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদির আগমন ঘটেছে।গণশিক্ষা আধার হিসেবে এগুলির গুরুত্ব আজ সার্বজনীন স্বীকৃত।
গণমাধ্যমের স্বরূপঃ
“গণ” কথাটির অর্থ হলো আপামর জনসাধারণ। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এই সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশ অক্ষর জ্ঞানহীন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের গ্রন্থ পাঠের কোনো সুযোগ নেই। ফলে এই সব সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষার জন্য সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত মাধ্যম গুলিই এক কথাই গণমাধ্যম। শোনা ও দেখা উভয়ের সংযোগে দূরদর্শন। এই দুই মাধ্যম মানুষের মনে সর্বাপেক্ষা গভীর ছাপ ফেলার ক্ষমতা রাখে।
গণমাধ্যম ও শিক্ষাঃ
সামাজিক পরিস্থিতিতে পিছিয়ে থাকা সর্বাধিক জনসমষ্টির মধ্যে চিন্তা ভাবনা ও বিশ্লেষণের বীজ রোপন করতে গণমাধ্যম গুলি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান।গণমাধ্যম গুলিই অর্ধশিক্ষিত মানুষের মনের অন্ধকার দুর করে। গণমাধ্যম গুলির সাহায্যে নিরক্ষর সাধারণ মানুষ দেশ বিদেশের মানুষ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত হয়। তাদের বিচিত্র ধরনের রীতি নীতি,আচার আচরণ ও ভাষা শুনতে পায়। তাদের সংকীর্ণ মন মুক্তি পায় বিশাল বিশ্বে। বিভিন্ন পেশার মানুষ গণমাধ্যমের সাহায্যে উপকৃত হয়। একজন সাধারণ কৃষক জানতে পারে উন্নত সার ও কীটনাশকের খবর, আবহাওয়া সম্পর্কে নানা প্রয়োজনীয় খবর।
বিভিন্ন গণমাধ্যম ও তাদের ভূমিকাঃ
বর্তমান সময়ে শিক্ষা বিস্তারে প্রধান গণমাধ্যম গুলি হল সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন।এই জ্ঞান নির্ভর যুগে শিক্ষিত জন মানুষে সংবাদ পত্র জীবনের দর্পণ স্বরূপ রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদির সম্পর্কে পরিচয় লাভের ফলে মানুষ দেশ বিদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে।
তবে শিক্ষা বিস্তারে দুটি মাধ্যম বিশেষ অগ্রগণ্য, যথা- বেতার ও দূরদর্শন। গ্রামীণ কর্মক্লান্ত নিরক্ষর মানুষ সারাদিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যায় রেডিওর সামনে বসে অবসর বিনোদন করেন। কৃষি কথার আসর , পল্লিকথা, চাষী ভাইদের জন্য অনুষ্ঠান, নাটক, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা জ্ঞান লাভ করে।
অন্যদিকে দূরদর্শন বস্তুকে মানুষের দৃশ্য পটে আনে এর ফলে মানুষ বাস্তব জ্ঞান লাভ করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। বর্তমানে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন একভাবে Teaching Aid এর ভূমিকা পালন করে। চরিত্র গঠন, নীতি , শিক্ষা, সাহিত্য বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক বোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্রের ভূমিকা অস্বীকার করার অবকাশ নেই।
গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতাঃ
গণমাধ্যমগুলির অবদান কার্যকরী হয় তখনই, যখন পরিচালক মন্ডলী জনদরদী সৎ ও নিষ্ঠাবান হয়। সাধারণ মানুষের মেজাজ, মর্জি, মন, মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত না হলে, উদ্দেশ্য কখনই সফল হতে পারেনা। সাধারণের সাথে অন্তরের সংযোগ অনুভব করতে না পারলে এধরনের শিক্ষা প্রয়োগের কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশনা ভাষার ব্যবহার, বিষয় নির্বাচনের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমগুলির এসব দিকেও নজর রাখা দরকার। সেই সাথে যুক্ত হওয়া দরকার রাজনৈতিক প্ররোচনা থেকে নিরপেক্ষতা অবশ্যই গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সুদৃঢ় করে।
উপসংহারঃ
নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গণ শিক্ষার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুলির অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যমের ভূমিকা আরও অনেক শক্তিশালী হওয়া দরকার।যেহুতু টেলিভিশন এর মতো শক্তিশালী মাধ্যমটি এখনও বহুলাংশে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীনে, সেহুতু সেসব পক্ষকেও এব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করছে শিক্ষা বিস্তারের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের সকলের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ করতে তা অত্যন্ত জরুরি।
বাংলার ঋতু বৈচিত্র
ভূমিকাঃ
মানবসভ্যতা যতই আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের জীবনে ততোই প্রকট হচ্ছে অশান্তির কালো মেঘ। জীবনের অশান্তির এই নিকষ কালো অন্ধকারে সুখের চেয়ে মানুষ আজ স্বস্তির ব্যাকুল অনুসন্ধানী। আমাদের প্রিয় প্রকৃতিতেই রয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষিত অনাবিল শান্তি ও স্বস্তির উপকরণ। সেজন্য এই আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে মানুষ মুক্ত প্রকৃতির রূপ ও বৈচিত্র্য আস্বাদের জন্য ব্যাকুল। প্রকৃতির বৈচিত্র্য জীবনকে করে তোলে বর্ণময়, আর রূপ জীবনের একঘেয়েমি দূর করে নতুন রঙে রাঙিয়ে দেয়। বাঙালির সৌভাগ্য যে, আমাদের স্বদেশ বঙ্গভূমিতে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। বছরের বারো মাসে ছয় ঋতুতে প্রকৃতির নতুন রূপে নতুন লীলা বাংলার মানুষের জীবনকে অনাবিল স্নিগ্ধ আনন্দে ভরিয়ে তোলে। বঙ্গভূমির প্রকৃতি প্রত্যেকটি ঋতুতে বাঙালির জীবনে এনে দেয় নব নব রূপ ও রসের অপরূপ ছন্দ। বাংলার এই অপরূপ রূপে মোহিত হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছিল-
“জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে – তুমি বিচিত্ররূপিনী”
বাংলার ঋতু বৈচিত্র্যঃ
বাংলায় প্রকৃতি সমগ্র বছরজুড়ে নানা ঋতুর সমাহারে বৈচিত্রের মধ্যে এক সার্বিক ঐক্য স্থাপন করে। প্রকৃতি বিশেষজ্ঞগণ প্রতিটি বছরকে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে মোট ছয়টি ঋতুতে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক ঋতু নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ও সমুজ্জ্বল। বছরের বারো মাসে প্রত্যেক দু মাস অন্তর এক একটি নতুন ঋতু জীর্ণ পুরাতনের অবসানে তার নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বাঙালির জীবনকে নানা বর্ণের ছটায় রাঙিয়ে দিয়ে যায়। সেই ছটায় প্রত্যেক বাঙালির জীবনে দুঃখ, কষ্ট, মন খারাপ, একঘেয়েমি দূর হয়ে আসে অনাবিল আনন্দের স্রোত। যদিও বর্তমানে প্রাকৃতিক দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর মত বিভিন্ন কারণে আর বাংলায় ছয়টি ঋতুর আবির্ভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না। বদলে আমরা কেবলমাত্র গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং শীত এই চারটি ঋতু অবস্থিতিকেই অনুভব করতে পারি। তবে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের ঋতু বৈচিত্রের উপর সভ্যতার এই আগ্রাসন এখনো সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি।
গ্রীষ্মকালঃ
“প্রখর তপন তাপে, আকাশ তৃষায় কাঁপে, বায়ু করে হাহাকার”
ঋতু-পরিক্রমার প্রথম ঋতু গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্ম হল ‘রুদ্র তাপস। রুক্ষ তার তনু। উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল।’ তৃতীয় নেত্রে অগ্নিস্রাবি দৃষ্টি। তার ‘লোলুপ চিতাগ্নি শিখায়’ আকাশ বাতাস মাটি হয় দগ্ধ। সূর্যের প্রখর তাপে প্রচণ্ড দাবদাহে বাংলার মাটি, খাল, বিল, নদী-নালা শুষ্ক হয়ে পরম তৃষ্ণায় সামান্য বর্ষার প্রতীক্ষা করতে থাকে। তবে এমন রুদ্র রূপ এর মধ্যেও প্রকৃতি গ্রীষ্মের ডালি ভরে দেয় চম্পক, রজনীগন্ধা সহ আম, জাম, কাঁঠালের মতো নানা সরেস ফল ফুল দিয়ে। অবশেষে প্রখর রুদ্র মূর্তিতে বর্ষার আবাহন করে জ্যৈষ্ঠের শেষে এর অবসান ঘটে।
বর্ষাকালঃ
গ্রীষ্মের অবসানে হাজির হয় ‘ঘন গৌরবে নবযৌবন বরষা।’ বর্ষা হল ঋতু-পরিক্রমার দ্বিতীয় ঋতু। রুদ্র তাপস গ্রীষ্মের রুক্ষ অগ্নিস্রাবি দৃষ্টি আর প্রখর দাবদাহে শুষ্ক প্রকৃতি যখন পরম তৃষ্ণায় কাতর, তখনই মেঘের দামামা বাজিয়ে আকাশ কালো করে ধরিত্রীর বুকে নেমে আসে অঝোর বর্ষণ। এই অঝোর বৃষ্টি ধারায় ভরে যায় খাল বিল,নদী, নালা। এই সময়ে প্রকৃতি আবার নব কলেবরে সজ্জিত হয়ে ওঠে। ফুটিফাটা মাটি, খাল-বিল, নদী-নালা, পশুপাখি সকলে প্রশান্তিময় শীতলতায় স্বস্তি ফিরে পায়। গ্রাম বাংলার বুকে কৃষকের মন নেচে ওঠে আনন্দে। জমিতে বীজ তোলা ও রোপণের ধুম পড়ে।
শরৎকালঃ
“শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী”
দুইমাস ব্যাপী বর্ষার অবসানে জল থৈ থৈ স্নিগ্ধ শীতল প্রকৃতির বুকে তৃতীয় ঋতু শরতের একটা আলাদা মাধুর্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে। ঘনকালো মেঘে জমে থাকা বর্ষণের বাষ্প পৃথিবীর বুকে অঝোর ধারায় ঢেলে দিয়ে এসময় আকাশ হয়ে ওঠে ঘননীল। পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আকাশের বুকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভেসে বেড়ায়। তারা অতি স্নিগ্ধ, প্রশান্ত; যেন আর তাদের কোন তাড়া নেই। মাঠে মাঠে প্রস্ফুটিত কাশগুচ্ছ প্রকৃতির সাজসজ্জায় এক অনন্য মাত্রা এনে দেয়। এমন স্নিগ্ধ, শীতল প্রকৃতির বুকে জীবনের একঘেয়েমি দূর করে বাঙালি মেতে ওঠে পুজা পার্বনে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবগুলি এসময় পালিত হয়ে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম হলো দুর্গোৎসব।
হেমন্তঃ
“হায় হেমন্ত লক্ষী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা-
হিমেল ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।”
কুয়াশার ঘোমটা টেনে বিষাদখিন্ন হৃদয়ে বৈরাগ্যের তপস্যায় বাংলার চতুর্থ ঋতু হেমন্ত থাকে নীরব। হেমন্ত যেন বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। কারণ অন্য কোথাও এর উপস্থিতি তেমন লক্ষ্য করা যায় না। এই হেমন্তেরই অগ্রহায়ণ মাসে আসে বাঙালির চির আকাঙ্খিত নবান্ন উৎসব। এসময় ধান কাটা শেষ হয়ে শুরু হয়; হয় চৈতালি ফসলের আয়োজন। শুকনো বাতাসে থাকে এক মন্থরতা। কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ এই দুই মাস ধরে হেমন্ত ঋতুর ব্যাপ্তি। এই দুই মাসে প্রকৃতি ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ শীতল থেকে আরো শীতলতর হতে থাকে। অবশেষে প্রকৃতিকে ঘাসের ওপর হীরের মতন চিকচিকে শিশির উপহার দিয়ে হেমন্ত বিদায় নেয়।
শীতকালঃ
“কার্তিকের এই ধানের খেতে
ভিজে হাওয়া উঠল মেতে
সবুজ ঢেউ’ইয়ের পরে।
পরশ লেগে দিশে দিশে
হি হি করে ধানের শিষে
শীতের কাঁপন ধরে।”
শিশির শয্যায় হেমন্তের অবসানে আসে শীত। শীতকালে পদে পদে জড়িয়ে থাকে শীতাতুর জড়তা। তবুও শীত বাঙালির উৎসবের; অত্যন্ত কাছের প্রিয় এক ঋতু। এই সময়ে বাঙালি মেতে ওঠে নানা ধরনের মিলন মেলায়। বাজারে আসে নতুন নতুন ফল ও সবজি। প্রকৃতির গাছপালা নিজের জীর্ণ পুরাতনকে ঝরিয়ে ফেলে নতুন রূপে সেজে ওঠার জন্য প্রস্তুত হয়।
বসন্তঃ
“বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির ‘পরে কী আদরে।
তাই সে ধূলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপ্রের সাজি আপনি ভরে কী আদরে।।”
সকল ঋতুর অবসানে বছরের অন্তিম লগ্নে আগমন ঘটে বসন্তের। এর উজ্জ্বল আলোর ধারায় চারিদিক হয় উদ্ভাসিত। শীতে ঝরে যাওয়া জীর্ণ প্রকৃতি নবকলেবর সেজে ওঠে। গাছপালাতে লাগে নতুন সবুজের ছোঁয়া। প্রস্ফুটিত শিমুল পলাশের অর্ঘ্যে আগমন ঘটে বাগদেবী সরস্বতীর। বাঙ্গালী গৃহবাসী দ্বার খুলে মেতে ওঠে নতুন রঙের খেলায়। আর কোকিলের কুহুতান এই অনাবিল আনন্দে এক নতুন মাত্রা যোগ করে দেয়।
উপসংহারঃ
বাংলার ঋতু পরিক্রমা কেবল প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের ধরাবাঁধা পটচিত্র মাত্র নয়। বাংলার ঋতুচক্র বাঙালির চেতনাকে মায়াময় কবিত্বে ভরে দিয়ে যায়। প্রকৃতির এই ঋতুচক্রে বাঙালির জীবন সুখ দুঃখে মিলেমিশে আবর্তিত হয়। ঋতুচক্রের কারণে যেমন প্রকৃতি নতুন নতুন সাজে সজ্জিত হয় তেমন কখনও অনাবৃষ্টির কারণ খরা বা কখনো অতিবর্ষনে বন্যাও হয়ে থাকে। বছরজুড়ে বৈচিত্র্যময় আবর্তনে এই ঋতুচক্র আমাদের যেন দুঃখকে জয় করে সুখের প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্রই শিখিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের মন যেনো গেয়ে ওঠে-
“মোরে আরো আরো দাও প্রাণ।”
উন্নয়ন বনাম পরিবেশ
ভূমিকাঃ
সভ্যতার অগ্রগতির এক অন্যতম লক্ষণ হল উন্নয়ন। উন্নয়নের ফলেই সভ্যতার আদিম রূপ নতুন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের এক নিবিড় সম্পর্ক। উন্নয়নের ফলে প্রাচীন রুক্ষ পরিবেশের সঙ্গে সমঝোতা করে এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি পরিবেশের উপর কালো থাবা বসিয়েছে। তারই কারণে উন্নয়নকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী পরিবেশে নানান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা গিয়েছে।
● উন্নয়ন বনাম পরিবেশঃ
উন্নয়নের ধারণাঃ
উন্নয়ন শব্দের অর্থ হল বিকাশ করা। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের গভীর সম্পর্ক। উন্নয়নের ফলে পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কারণ সভ্যতার প্রয়োজনীয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নয়ন পরিবেশের স্বাভাবিকত্ব হরণ করতে থাকে। ফলে, প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার সীমিত হয়ে আসে। পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি, দূষণ ইত্যাদি বেড়ে চলে।
সভ্যতার উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারঃ
বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির যুগে সভ্যতার কৃষি ও শিল্প নির্ভরজীবন অনেকাংশেই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য রাসায়নিক কীটনাশক সারের ব্যবহার পরিবেশের জল, মাটি দূষিত করছে। শিল্পের উন্নয়ন দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটায় শিল্পোন্নয়নের জন্য ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস করে কারখানা স্থাপন হচ্ছে। এর পাশাপাশি শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও বর্জ্য পদার্থ পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে।
পরিবেশের উপর উন্নয়নের প্রভাবঃ
সভ্যতার ক্রমোন্নতির পথে পরিবেশের উপর উন্নয়নের প্রভাব সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস, প্রাকৃতিক শক্তির নিঃশেষণ, কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস, বৃষ্টিপাতের অভাব, পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যে ব্যাঘাত উন্নয়নকে বিঘ্নিত করছে। ফলে বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্য নাগরিক সাচ্ছন্দ্যও হচ্ছে প্রভাবিত। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের উন্নয়নের যোগাযোগ কতটা সেই প্রশ্নও ওঠে।
উন্নয়নের স্বরূপঃ
প্রকৃতির স্বাভাবিক সত্তার সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর সহাবস্থানেই সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিক পরিবেশে সভ্যতার উন্নয়নে পরিবেশের অবনমনকে প্রতিহত করতে কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন—
(ক) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
(খ) সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
(গ) ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।
(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা।
(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ।
উপসংহারঃ
আধুনিক সভ্যতার দুর্বার গতিতে উন্নয়ন স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন এবং পরিবেশের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধানেই পৃথিবী সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠবে।
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা
ভূমিকাঃ
“মাতৃভাষা সে তো মাতৃদুগ্ধ সমান, সে ভাষায় শিক্ষালাভে ভরে উঠে প্রাণ”
মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান। মাতৃভাষায় মনের ভাব যত সহজে প্রকাশ করা সম্ভব, অন্য কোনো ভাষায় তা নয়। জ্ঞানবিদ্যার চর্চায়ও মাতৃভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক। যে ভাষায় সহজেই সব কিছু বলা-কওয়া ও বোঝানো যায়, সেই ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। এই জন্যই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে আমাদের বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষাটা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া দরকার।
মাতৃভাষা সমস্যাঃ
ভারত নানা ভাষার দেশ। তাই শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে বাস্তব অসুবিধা আছে। তাহলে একে অপরের সাথে যোগসূত্র কীভাবে রক্ষিত হবে? ভারতে ১৫টি ভাষা সংবিধানে স্বীকৃতি পেলেও ভারতে ভাষার সংখ্যা ১৭৯ এবং উপভাষার সংখ্যা ৫৪৪। ভারতে এতগুলি ভাষা থাকার জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার যথার্থ অসুবিধা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষাই এই ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণের উপায় হতে পারে। জোর করে অন্য ভাষা চাপিয়ে দিলে সমস্যা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে।
শিক্ষার বাহনঃ
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবি উঠেছে। এই দাবি ন্যায়সংগত। তাই অঞ্চল ভিত্তিতে এক-একটি ভাষা প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতে এখন অঞ্চল ভিত্তিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।
ইংরেজি ভাষাঃ
তবে আমাদের দেশে একমাত্র মাতৃভাষাই সর্বশিক্ষার উপযুক্ত বাহন হতে পারে না। বহু ভাষাভাষী দেশ হওয়ায় যোগাযোগ ও জ্ঞান বিনিময়ের ভাষা রূপে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতে দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।” এদিকে ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র রাখতে গেলে ‘হিন্দি’ ভাষা শেখা আমাদের পক্ষে একইরকম জরুরি। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে এটি খুবই দরকার।
উপসংহারঃ
‘Mass Education’-এর জন্য অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাই যথেষ্ট। কিন্তু, উচ্চতর শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। তা না-হলে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার যুদ্ধে আমরা হেরে যাব। আমাদের দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে। ভারত বিশ্বসভার আসন থেকে বঞ্চিত হবে।
বাংলার উৎসব
সুজলা-সুফলা যে বাংলাদেশের ছবি বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন তার বিপরীত প্রান্তের অন্য এক ছবি এঁকেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তীও –‘শিশু কাঁদে ওদনের তরে’। আসলে বাঙালি সুখ-সম্পদশালী বোধ হয় কোনোদিনই ছিল না। তাই বাঙালি পরিবার মানেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে হরিহর-সর্বজয়ার (পথের পাঁচালী) পরিবার। এ জীবনে অভাব আছে, দারিদ্র্য আছে। মহামারি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাকে বারবার বিপন্ন করেছে। তবু বাঙালি বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে প্রাণের স্পন্দনে, উৎসবে। বাঙালি এই উৎসবের রঙিন দিনগুলি থেকেই সঞ্চয় করে নিয়েছে তার বাঁচার উপাদান।
একঘেয়েমি বাংলা দেশ হল উৎসবের দেশ। বাংলার উৎসবগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালির ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের দূর করে এক ঝলক মুক্ত হাওয়া বয়ে আনে উৎসব। মানবজীবনে উৎসব নানা রং নিয়ে আসে। রোজকার রুটিনে-বাঁধা জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে সকলেই তাই খুশিতে মেতে ওঠে। সাময়িক বিরাম মানুষকে নতুন উদ্যমে কর্মজগতে ফিরিয়ে আনে। “আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক, আমার শুভ সকালের শুভ হোক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি”— এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। মানবজীবনে উৎসবের প্রভাব প্রতি মুহূর্তে বোঝা যায়।
২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫ বৈশাখ, ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন, ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন ইত্যাদি দিনগুলি হল জাতীয় উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। প্রজাতন্ত্র দিবসে ও স্বাধীনতা দিবসে সমগ্র জাতির চেতনায় এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।
বাঙালি শুধু ধর্মীয় আবেগপ্রবণ জাতি নয়, সেই ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে তার নানা পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান। যেমন অন্নপ্রাশন, বিবাহ, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত এই উৎসবগুলিতে সমগ্রভাবে গোটা বাঙালি সমাজ যুক্ত না-হলেও বহু মানুষই এগুলিকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। নানা ঋতুকে ঘিরেও উৎসবে মেতে ওঠে বাঙালি। বর্ষামঙ্গল, পৌষমেলা, নবান্ন, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, নববর্ষের মতো নানা ঋতুকেন্দ্রিক উৎসবের মধ্য দিয়ে দুঃখ-দারিদ্র্য অভাবপীড়িত বাঙালি নতুন করে নব আনন্দে জেগে ওঠে।
ধর্মাবলম্বী মানুষের বাংলা দেশ বিভিন্ন ধর্মের লীলাভূমি বাসস্থান। এখানকার ধর্মীয় উৎসব তাই বিচিত্র। হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল দুর্গোৎসব। দুর্গাপুজো শুধুমাত্র পুজো নয়, এটি এখন একটি জাঁকজমকপূর্ণ জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। দুর্গোৎসব ছাড়া রথযাত্রা, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, সরস্বতীপুজো প্রভৃতি উৎসবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকগুলি পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতিরও আয়োজন হয়। মুসলমানদের উৎসবগুলির মধ্যে মহরম, ইদ, বকরি ইদ, সবেবরাত, সবেমিরাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব হল বড়োদিন। এ ছাড়া, বৌদ্ধগণ বুদ্ধপূর্ণিমা, জৈনগণ পরেশনাথের জন্মদিন এবং বৈয়বগণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথি সাড়ম্বরে পালন করেন।
অতীতে বাঙালির উৎসবের মধ্যে হয়তো বর্তমানের মতো জাঁকজমক বা আড়ম্বরের প্রাধান্য ছিল না, কিন্তু ছিল প্রাণের স্পন্দন, সেখানে ছিল না অর্থকৌলিন্যের প্রকাশের রেষারেষি। সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে উঠত মধুময়। তাই সেদিন একের উৎসব সহৃদয়তার গুণে আপামর সকলের উৎসবে পরিণত হত। এখন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক অবস্থারও; মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানসিকতায় এসেছে পরিবর্তন। তাই উৎসবের রূপ, মেজাজ ও উপস্থাপনায় ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। উৎসব হয়েছে হুজুগপ্রিয়, জাঁকজমক ও আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। অভাব ঘটেছে উৎসবের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতায়। মানুষের অন্তরের শুভ আকুতি গেছে হারিয়ে। পারস্পরিক জাঁকজমক প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে সার্বজনীন পূজা-উৎসবে বেড়েছে চাঁদার দৌরাত্ম। এখন বহুক্ষেত্রে উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে মধ্যবিত্তের অন্তরে আতঙ্কস্বরূপ নিতান্ত স্থানীয় পরিবেশে, লৌকিক প্রয়োজনে বাংলার নিজস্ব উৎসবগুলির সৃষ্টি। চড়ক পুজো, গাজন উৎসব, শীতলা, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি পুজো বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির অঙ্গ।
পরিশেষে বলতে হয়, উৎসব হল আনন্দের উৎসধারা। উৎসবে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়। মানুষের মিলনের কেন্দ্ররূপে উৎসবের গুরুত্ব বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য। মানুষে মানুষে যে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-উচ্চ-নীচ ভেদ দেখা যায়, উৎসব সেইসব ভেদরেখা দূর করে মানুষকে মহামিলনের ঐক্যকেন্দ্রে এক হতে জানায় আহ্বান। এখানেই সামাজিক উৎসবগুলির প্রধান তাৎপর্য।
চরিত্র গঠনে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা
বহু প্রাচীন প্রবাদেই বলা আছে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার কথা- ‘সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বাস’। আর সুস্থ সবলতার একমাত্র উৎস হল খেলাধুলা। মানবসভ্যতার ক্রম বিবর্তনের দেশে দেশে যুগে যুগে খেলাধুলার নানা রূপান্তর হয়েছে। সবরকম খেলাধুলাই মানুষকে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারি করে জীবনে জয় এনে দেয়।
একটা আদর্শ ছাত্রের প্রধান কর্তব্য যেমন পড়াশোনা তেমনি খেলাধূলাও। শরীরচর্চার ফলে দুর্বল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল হয়। খেলাধুলায় শরীরচর্চার সঙ্গে আনন্দও মেলে।
‘Health is wealth’– স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্যবান দেহ হয় সুখ সম্পদের অধিকারী, সৌন্দর্যের আকর। স্বাস্থ্য বিকশিত না হলে কোনো কর্মই সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে না। তাই স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে খেলাধুলা একাএকান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়- “All work and no play makes Jack a dull boy.”
খেলাধুলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-
ব্যক্তির চরিত্র গঠনে খেলাধুলার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষের চরিত্রে দৃঢ়তা আসে। খেলাধুলা করতে ধৈর্য ও সংযম উভয়েরই প্রয়োজন হয়। ফলে যারা খেলাধুলা করে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও চরিত্রের মধ্যে এই দুটির ছাপ পড়ে। খেলাধুলা সহমর্মিতা ও সহানুভূতি বোধের জন্ম দেয় । খেলাধুলার মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্রে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়, অধ্যবসায়ের মতো মানসিক গুণাবলীগুলো যুক্ত হয়। এছাড়া খেলাধুলা মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়া অভ্যাস গড়ে তোলে।
ছাত্রজীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব অসীম। তাই স্কুল কলেজের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শারীরশিক্ষা। খেলাধুলা শিক্ষার্থীকে শেখায় বিনয়ী হতে এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করতে। খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা আলোচনায় বলা যায়-
শিশুর মানসিক বিকাশে খেলাধুলার ভূমিকা খুবই সহায়ক ও স্বতঃস্ফূর্ত। খেলাধুলার ফলে যে আনন্দময় পরিবেশে শিশু বড়ো হয় তা তাকে উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত, আনন্দমুখর করে তোলে। এর ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ সহজ ও সাবলীল হয়।
খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি হয়। খেলার মধ্যে সৃষ্ট পরস্পরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতা মানুষের ভেতরে সম্পর্ক তৈরি করে। সেই সম্পর্ক সহযোগিতার, সৌহার্দ্যরে ও সম্প্রীতির।
খেলাধুলা মানুষের ভেতর জাতীয়তাবোধ তৈরি করে। কারণ খেলাধুলা এমন একটি বিষয় যা ধর্ম, বর্ণ, জাত, রাজনৈতিক পরিচয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই।
অতীতকাল থেকেই একটি দেশের সাথে অন্য একটি দেশের সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান সময়েও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে খেলাধুলা কার্যকর একটি মাধ্যম।
খেলার মাঠ পুরো বিশ্বকে এক জায়গায় নিয়ে আসে। বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে এসময় মেলবন্ধন তৈরি হয় বলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়।
অতিরিক্ত কোনো কিছুই মানুষের জন্য ভালো নয়। অতিরিক্ত খেলাধুলা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা রেখে শুধুমাত্র খেলাধুলায় মগ্ন হয়ে পড়ে। এতে করে তাদের শিক্ষাজীবন ব্যহত হয়। অতিরিক্ত খেলার ফলে সময়, অর্থ, শ্রমের অপচয় হয়।
শরীর ও মন পরিপূর্ণভাবে উজ্জীবিত করতে খেখেলাধুলা অন্যতম বিবিষয়। খেলাধুলা যেমন নির্মল আনন্দ দেয় তেমনি জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে। শুধু তাই নয় খেলাধুলা ব্যক্তিকে নাম, যশ, খ্যাতি, অর্থ এনে দেয়। মানুষকে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। পারস্পরিক তিক্ততা দূর করে মনে প্রশান্তি এনে দেয়। তাই পৃথিবীব্যাপী খেলাধুলার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
কন্যাশ্রী প্রকল্প
ভূমিকাঃ
রবীন্দ্রনাথ প্রায় একশো বছর আগে লিখেছিলেন-
“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?”
—কবির এই প্রশ্নের উত্তর একবিংশ শতকের স্বাধীন ভারত তথা বাংলা আজও খুঁজে পেয়েছে কি? এখনও দেশের অধিকাংশ মেয়ে শিক্ষার মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতি অল্প বয়সেই নিতান্ত সাংসারিক সামগ্রী হিসেবেই বিবেচিত হয়। এখনও কন্যাভ্রুণ হত্যা কিংবা বাল্যবিবাহের মতো নির্দয়তা সমাজে স্বীকৃত। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। এখনও মেয়েদের এগিয়ে চলার পথ প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। মাত্র কয়েক বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গ বাল্যবিবাহে দেশের পঞ্চম স্থানে ছিল। বালিকাদের মধ্যে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার হারও ছিল যথেষ্ট বেশি। এই প্রবণতা আটকাতে এবং মেয়েদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে রাজ্য সরকার চালু করে ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প।
প্রকল্পের নিয়ম, উৎস ও বাস্তবতাঃ
কন্যাশ্রী প্রকল্প অনুসারে, যেসব পরিবারের বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম, সেই পরিবারের ১৩ থেকে ১৮ বছরের ছাত্রীরা বছরে ৫০০ টাকা করে (এখন বেড়ে হয়েছে ৭৫০ টাকা) বৃত্তি পাবে। যদিও অনাথ বা প্রতিবন্ধী ছাত্রীদের ক্ষেত্রে আয়ের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। শিক্ষার মূলস্রোতে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে গেলে এই ছাত্রীরা ১৮ বছর বয়সে পাবে এককালীন ২৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ কোনো মেয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের লক্ষ্যপূরণের জন্য সরকার তার পাশে দাঁড়াবে। এই প্রকল্পের জন্য এখন রাজ্য সরকারের বছরে খরচ হচ্ছে ৮৫০ কোটি টাকা। আগামী বছরগুলিতে এই ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনাই আরও বেশি। রাজ্যের প্রায় ২০ লক্ষ ছাত্রী এই সুবিধা পাচ্ছে। এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে সংখ্যাটা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে।
এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা জরুরি, বছরে ৫০০ টাকা হয়তো খুব বিরাট অঙ্কের টাকা নয়, কিন্তু সেই টাকাটাও যে ছাত্রীর প্রাপ্য, তার জন্যই খরচ করা হচ্ছে কি না সেই ব্যাপারেও একটি সরকারি নজরদারি থাকা জরুরি। ১৮ বছরের কন্যাকেও যখন সরকার ২৫ হাজার টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে দেবে, সেখানেও এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে মেয়েদের শুধু অধিকার দিলেই হবে না, তা রক্ষা করা হচ্ছে কি না, সেটা দেখাও সরকারের দায়িত্ব। উল্লেখ্য নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির স্বার্থে সরকার যখন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন জনমানসে তার একটি সদর্থক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
উপসংহারঃ
‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প পৃথিবীর বহু জায়গায় একটি উন্নতমানের কল্যাণকামী প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকারের খেয়াল রাখা উচিত তা যেন নজরদারির অভাবে ব্যর্থ না-হয় এবং অবশ্যই বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণও আরও কিছুটা বাড়ালে ভালো হয়। ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্পের ফলে সুফল কতটা ফলল, মাঝপথে স্কুলছুটের সংখ্যা কতটা কমল, বাল্যবিবাহ কতটা রোধ হল, তা বিচারের সময় এখনও আসেনি। তবে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে অনেকেই মনে করছেন, পরিবর্তন চোখে পড়ছে, কমছে স্কুলছুটের প্রবণতা। তাই এই প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হলে সুফল পাওয়া যাবে, সমাজের বিরাটসংখ্যক পিছিয়ে পড়া অংশের মেয়েরা অদূর ভবিষ্যতে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করবার অধিকার অর্জন করবে; এমনটা আশা করাই যায়।
দূরদর্শনের প্রভাব
“প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।”- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভূমিকাঃ
অত্যাধুনিককালের গণজাগরণ ও চিত্ত বিনোদনের প্রধান স্তম্ভ ১৯২৬-এ ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড আবিষ্কৃত দূরদর্শন যা বিজ্ঞানলালিত যন্ত্রসভ্যতার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। গ্রিক ‘টেলি’ অর্থাৎ ‘দূর’ এবং ‘ভিশন’ অর্থাৎ ‘দৃশ্য’- এদের যুগলবন্ধনে ‘টেলিভিশন’ ও ‘দূরদর্শন’ শব্দের সৃষ্টি। দূরদর্শনের ঐন্দ্রজালিক শক্তির বলে দূর হারিয়েছে তার দূরত্ব, অপরিচিত হয়ে উঠেছে অতি পরিচিত, চির আপন।
শিক্ষার বিস্তার ও দূরদর্শনঃ
গণশিক্ষার মাধ্যম রূপে দুরদর্শনের ভূমিকা অবিসংবাদিত। বহু নিরক্ষর মানুষ যারা সংবাদপত্র কিংবা পুস্তকপাঠে অপারক তাদের ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা লাভের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে দূরদর্শন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে ঘরে বসে বিশ্বের নানান আবিষ্কার, শিল্প-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় দূরদর্শনের কল্যাণেই। বর্তমানে ডিজিট্যালাইজেশনের যুগে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অডিয়ো-ভিশুয়াল পদ্ধতি প্রয়োগের দরুন দূরদর্শনের প্রবেশ ঘটেছে শিক্ষাঙ্গনেও।
সামাজিক ক্ষেত্রে দূরদর্শনের ভূমিকাঃ
দূরদর্শনের প্রভাবে নানা কর্মব্যস্ততার ফাঁকে মানুষ যেমন নির্ঝঞ্ঝাট স্বস্তিলাভে সমর্থ হয় তেমনই উপভোগ করতে পারে বহু দূরদেশে সম্ভাবিত খেলার মজা, পদার্পণ করতে পারে শিল্প-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের বহুমুখী অঙ্গনে। আমেরিকার ধ্বংসাত্মক গোলাবর্ষণ হোক কিংবা কোনো পল্লিপ্রকৃতির অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোনো কিছুই দুরদর্শনের দর্শনশক্তির বহির্ভূত হতে পারে না।
দূরদর্শনের সাংগঠনিক ভূমিকাঃ
দূরদর্শন একটি বিশিষ্ট প্রচারমাধ্যম রূপে খুব সহজেই জনসচেতনতার প্রকাশক হয়ে ওঠে। দূরদর্শনের কল্যাণে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী কিংবা প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানসূচির ভিত্তিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খবরাখবর, সংবাদ সমীক্ষা, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন সম্প্রচারিত হতে পারে। তা ছাড়া দূরদর্শনের দ্বারা প্রচারিত নির্বাচনি প্রচার সংক্রান্ত খবরাখবর, সরকারি ঘোষণাসমূহ ইত্যাদি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়ে তাদের মধ্যে সংগঠনশীল মনোভাবের জন্ম দেয়।
দূরদর্শনের সুপ্রভাবঃ
আধুনিক বিদ্যুৎ-যুগে প্রমোদ বিতরণের মাধ্যম রূপে দূরদর্শনের প্রচারগত সুবিধা নানামুখী—
১) যে কোনো নবোদ্ভাবিত বিষয় অল্প সময়েই দূরে সঞ্চারিত হয়।
২) দূরদর্শনের মাধ্যমে একসঙ্গে বহু মানুষ জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।
৩) এর মাধ্যমে লাইভ ব্রডকাস্ট যেমন সম্ভব তেমনই যে-কোনো অনুষ্ঠানের রেকর্ড রাখা যায় ভিডিয়ো টেপরেকর্ডারের দ্বারা।
৪) দূরদর্শনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠি।
৫) মানবতাবোধের জাগরণ ঘটিয়ে সম্প্রীতি ও সংহতিবোধের প্রসার ঘটায় দূরদর্শন।
দূরদর্শনের কুপ্রভাবঃ
১) দূরদর্শন শিশুমনে অপরাধবোধ ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিপথগামিতার স্পৃহা সৃষ্টি করে।
২) দূরদর্শনের তীব্র প্রভাব মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করে দেয়।
৩) এটি শিক্ষার্থীদের মনকে চঞ্চল করে তোলে, ফলে তারা পঠনপাঠনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
৪) দূরদর্শন সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সময় ও বাস্তবতাবোধ নষ্ট করে দেয়।
৫) সর্বোপরি, দূরদর্শনে যৌনতার প্রচার যুবসমাজ তথা অপ্রাপ্তবয়স্কদের পতনমুখী করে তুলছে।
সরকারের ভূমিকা ও মানোন্নয়নঃ
রুচিশীল, দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির জন্য দূরদর্শনের মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানগুলির মানোন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সর্বাগ্রে সরকারকে সচেতন হয়ে দূরদর্শনের প্রচারব্যবস্থাকে সংহত করতে হবে। বর্তমানে অবশ্য দূরদর্শন ও বেতারের প্রচার এবং পরিচালনার দায়িত্ব ‘প্রসার ভারতী’ নামক এক সরকারি সংস্থার অধীনস্থ। ‘প্রসার ভারতী’-র একনিষ্ঠ প্রয়াসে ১৫ ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে DTH বা Direct to Home Service-এর সূচনা দূরদর্শন সম্প্রচারণে সংহতিসাধন করেছে।
উপসংহারঃ
শত বাধাবিপত্তি ও কুফলপ্রদায়ী শক্তির প্রভাব সত্ত্বেও গণশিক্ষার মাধ্যম রূপে দূরদর্শন অত্যন্ত মূল্যবান। একে আরও বেশি শিক্ষামূলক ও সক্রিয় করে তুলতে পারলে দূরদর্শন তার যথার্থ অর্থ নিয়ে আমাদের কাছে ধরা দেবে।
বিশ্ব-উষ্ণায়ন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়
ভূমিকা :
পৃথিবীর সামনে আজ ঘোর বিপদ। পৃথিবী আজ ভালো নেই। বিশ্ব পরিবেশ আজ গভীর সংকটের মুখে। আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীটি আমাদের সকলকে নিয়ে যুগযুগান্তর ধরে সূর্য প্রদক্ষিণ করে পরম শান্তিতে চলছিল। সেই পৃথিবী আজ ভয়ংকর এক সংকটের মুখে। এর কারণ পৃথিবীর উয়তা বাড়ছে।
উষ্ণায়নের পরিমাণ :
বিশ্ব উয়ায়ন নিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন। তাঁরা দেখছেন, গত শতাব্দীতে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল ০.৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই শতাব্দীতে আরও ১.১ ডিগ্রি সেলিসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লেই পৃথিবীর ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রজাতির জীবন বিপন্ন হবে। মেরু অঞ্চলে বরফ গলবে এবং পাহাড়ে পাহাড়ে যে হিমবাহ গলতে শুরু করেছে, তা গলতেই থাকবে।
বিষাক্ত গ্যাস ও তার পরিণাম :
পৃথিবীর এই উন্নতা বৃদ্ধির কারণ কিন্তু আমরাই। আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের যথেচ্ছ বিধ্বংসী আবিষ্কার আমাদের পৃথিবীর ‘গ্রিনহাউস’ গ্যাসকে বাড়িয়ে তুলে পৃথিবীর শ্বাসরোধ করে তুলেছে। এই গ্রিনহাউস গ্যাসে রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, বিভিন্ন ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ইত্যাদি। এরা পৃথিবীর উপর বিকীর্ণ তাপরশ্মিকে শোষণ করে নেয়, তাদের বেরোতে দেয় না, ফলে ভয়ংকর এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।
গ্লোবাল ওয়ার্নিং :
ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ, শিল্পায়ন, অরণ্যনিধন সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আকস্মিক উষ্মতা বৃদ্ধি ঘটছে, যা পরিবেশে সংকট সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের এই উষ্মতা বৃদ্ধিই গ্লোবাল ওয়ার্মিং নামে পরিচিত।
বায়ুমণ্ডলের উন্নতা বৃদ্ধির চরম ক্ষতিকর প্রভাব :
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আকস্মিক উন্নতা বৃদ্ধির ফলে মেরু প্রদেশের বেশ কিছু অংশের বরফ গলে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমুদ্রে জলস্ফীতি ঘটবে। বিজ্ঞানীদের মতে, এক মিটার সামুদ্রিক জলস্ফীতিতে ভারতের উপকূল অঞ্চলের প্রায় ১,৭০০ বর্গকিলোমিটার কৃষিক্ষেত্র জলমগ্ন হবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আকস্মিক উন্নতা বৃদ্ধির ফলে মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং আমেরিকা মহাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ১,১০০ প্রজাতির প্রাণীর চিরতরে বিলুপ্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং বর্তমান শতাব্দী শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই বিশ্বের ৭০% পানীয় জলের উৎস প্রায় কোনো তুষার হিমবাহই আর অবশিষ্ট থাকবে না। শুধু তাই নয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে মেরু প্রদেশের বরফ গলার ফলে বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং গোটা সুন্দরবন সহ ভারতের বেশ কিছু সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল এবং সম্পূর্ণ মালদ্বীপ সমুদ্রের জলের তলায় চলে যাবে, যার ফলে উদ্বাস্তু হবে পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি মানুষ।
প্রতিকারের উপায় :
নানারকম ভাবনাচিন্তা করে এই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে এই সংকট থেকে বাঁচাতে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশে দেশে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ‘বসুন্ধরা’ সম্মেলনে তা গৃহীতও হয়েছে। গাছপালা লাগিয়ে গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, ওজোন স্তরের ছিদ্র মেরামত করতে হবে, কলকারখানা থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া ছাড়া যাবে না। কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি বাতাস দূষিত করতে না পারে, তা দেখতে হবে। এইভাবে সংযত হতে পারলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিকে অনেকাংশে রোধ করা যাবে। খানিকটা কমতে পারে। এ ছাড়া বিশ্ব সংকটের হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই।
উপংসহার :
বিশ্বায়নের পর বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে তেল ও অস্ত্রের যে গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েছে, সেক্ষেত্রে পৃথিবীর উয়তা বৃদ্ধি নতুন মোড় নিয়েছে। উন্নয়নের নামে সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে পরিবেশ। এই বিপন্নতার হাত থেকে মুক্তি পেতে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে, নইলে পৃথিবীর বিপন্নতার জন্য আমরাই দায়ী থাকব।
শীতের সকাল
ভূমিকাঃ
ঋতুর যেমন ভিন্নতা, সকালেরও তেমনই ভিন্নতা। ঋতুর যেমন বৈচিত্র্য, সকালেরও তেমনই বৈচিত্র্য। ভিন্ন ঋতুর ভিন্ন সকাল। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র সাজ। স্বতন্ত্র চরিত্র। আবার শীত ঋতুরই সব দিনের সকাল একরকম নয়। এখন শীতের মাঝামাঝি। প্রকৃতির এক উদাসী, বিষন্ন চেহারা। সর্বাঙ্গে ধূসর পাণ্ডুরতার আবেশ। গাছে গাছে পাতা ঝরার ডাক। রোজ যেমন সকাল হয়, আজও তেমনই সকাল হয়েছে। কিন্তু আজকের সকালটা অন্য দিনের চেয়ে একটু আলাদা।
একটি দিনের সকালঃ
চোখে তখনও ঘুমের আবেশ। কত বেলা হয়েছে বোঝা যায় না। দরজা জানলা সব বন্ধ। বিছানায় লেপের উষ্ণতা ছেড়ে বাইরে আসতে মন চায় না। আরও, আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার আলসেমি ভর করে। এরই মধ্যে মা দুবার তাড়া লাগিয়েছে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার শব্দ। আজ রোববার। তবু উঠতে হলো। আজকের ঠাণ্ডাটা আরও কনকনে। লেপের আরাম ছেড়ে উঠে পড়লাম। জানলা খুলে দিতেই মুঠো মুঠো হিমেল হাওয়া ঘরে ঢুকল। বাইরে কুয়াশার ঘন চাদর। দূরের জিনিস চোখে পড়ে না। রোদের তেজ ঝিম-ঝিম। বাইরে আসতেই শীত-বুড়ী আমার শরীর ছুঁয়ে চলে গেল। শীতের হাওয়ার পরশ শুধু আমলকির ডালে ডালেই লাগে না, আমার শরীরেও শীতের কাঁপুনি। চাদর জড়িয়ে কলতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। জল নয়, যেন বরফ। গায়ে ঠাণ্ডার কামড়। এবার বারান্দায় এসে বসলাম। একটু পরে চা এলো।
সকালের ছবিঃ
ঘন কুয়াশা এখন একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করেছে। উত্তুরে হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আস্তে আস্তে কুয়াশার চাদরটা সরে যাচ্ছে। রাস্তা ভিজে গেছে। এরই মধ্যে লোকজন যে যার কাজে চলেছে। সবার গায়েই চাদর, গরম পোশাক। সামান্য দূরে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে একটা বাচ্চা ছেলে শীতে কাঁপছে। একটু রোদের জন্যে হা-পিত্যেশ করে অপেক্ষা করছে। গায়ে সাধারণ একটা জামা। চোখ সরিয়ে নিলাম। আকাশে সূর্য উঁকি মারল। রোদ ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু রোদে সেই ঝাঁঝ নেই। এবার বোঝা গেল অনেক বেলা হয়েছে। বারান্দা থেকে সামনের পার্ক দেখা যায়। সেখানে গাছে গাছে এখন পাতা ঝরার খেলা শুরু হয়েছে। কেমন এক বিবর্ণ, ধূমল চেহারা। পার্কে ছেলে বুড়ো অনেকেই ঘোরাঘুরি করছে। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। শব্দ করছে। এরই মধ্যে মাইক বাজিয়ে হই-হুল্লোড় করতে করতে অনেকে চড়ুইভাতি করতে চলেছে। কোথাও ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা ফুল ফুটে আছে। আরও নানান মরসুমী ফুলের বাহার। কেউ চলেছে চিড়িয়াখানা। গায়ে নানা রঙের পোশাক। কেউ চলেছে ফুলকপি, পালং, টমাটো আরও নানা সবজির বোঝা মাথায় নিয়ে।
সকালের ভাবনাঃ
এসব ছবি দেখতে দেখতে কখন যেন আনমনা হয়ে যাই। মনে মনে কত কথার মালা গেঁথে চলি। কবির চোখে শীত বৈশ্য। তার কেবলই সংগ্রহের নেশা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে শীতের গ্রামবাংলা। মাঠে মাঠে ধান কাটা হয়ে গেছে। কিষাণ চলেছে মাঠের পথে। মুগ, মুসুর, ছোলা, কলাই বোনার সময় যে বয়ে যায়। গাঁয়ের বধূ চলেছে ঘাটের পথে। শীতে খেজুর রসের গুড় তৈরির কাজ চলছে। আবার শহরে শীতের অন্য রঙ, অন্য সাজ। এখানে শীত আসে খুশির মেজাজ নিয়ে। আসে শহরকে নানা সাজে, নানা রঙে সাজাতে। শীতের মরশুমে শহরে খেলাধুলোর আসর বসে। শীত মানুষকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। সার্কাসের তাঁবু পড়ে শহরের উত্তর-দক্ষিণে। চড়ুইভাতি হাতছানি দেয়। চিড়িয়াখানা ডাকে। শীত আসে শহরকে নতুন করে উজ্জীবিত করতে।
উপসংহারঃ
শীতের সকাল আমার মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে। সেই পাতা-ঝরা, কুয়াশা-মোড়া সকালের দিকে তাকিয়ে মন কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। তখন শীতকে আমার এক উদাসী বাউল বলে মনে হয়। তার হাতে একতারা, সেখানে বৈরাগ্যের সুর। কিন্তু এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। পরক্ষণেই মনে হয় শীতের সকাল আমাকে আরও এক প্রাণচঞ্চল জীবনের কথা বলে যায়। শীত এসে মানুষকে আরও আনন্দমুখর করে তোলে। মানুষ তখন নানাসাজে নিজেকে আরও মনোহর করে তোলে। শীতের সময়ই নানা মেলা, নানা পার্বণ। শীত এসে মানুষের নিরানন্দের ঢাকনাটাকে কখন সরিয়ে দেয়। মানুষের মনে তখন খুশীর ছোঁয়া। শীতের সকালের কাছে এ আমাদের বড় পাওনা।
বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ
ভূমিকাঃ
বিজ্ঞানই একদিন আমাদের মন্থর, শ্লথগতি জীবনে এনেছে দুর্বার গতি। বিজ্ঞানই মধ্যযুগের তিমির আবরণ ভেদ করে আমাদের নিয়ে এসেছে আধুনিকতার স্বর্ণদীপ্ত উষার দ্বারপ্রান্তে। বিজ্ঞানীর অতন্দ্র সাধনায় একটার পর একটা রহস্যের জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। মানুষের হাতে এসেছে একের পর এক সম্পদ বৈভবের সহজ অধিকার। জীবন-যাপনে এসেছে তার অনিবার্য পরিবর্তন। জলে স্থলে মহাশূন্যে মানুষের অধিকার হয়েছে বিস্তৃত। কেবলই আবিষ্কার-উদ্ভাবনে আর তার প্রয়োগে মানুষ হয়েছে দিশেহারা। বিজ্ঞান আধুনিক জীবনযাত্রার অপরিহার্য দোসর। ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ব্যাপকতা আজ অবিস্মরণীয়। বিজ্ঞানের অমিত শক্তির আশীর্বাদে মানুষ ধন্য হয়েছে। আবার তার ভয়ঙ্কর ভয়াল রূপ প্রতক্ষ করে মানুষ হয়েছে ত্রাসগ্রস্ত।
মানুষের কল্যাণেই বিজ্ঞানের আবিষ্কারঃ
মানুষের অনন্ত কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসাই মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে নব নব ঐশ্বর্যের দিগন্ত। এতে শুধু তার জ্ঞানভাণ্ডারই সমৃদ্ধ হয়নি, অন্ধবিশ্বাস আর প্রথাচারের আনুগত্যের অবসান হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে এক অনন্ত শক্তির অধিকার। এই অমিত শক্তির অধীশ্বর হয়েই মানুষ দিকে দিগন্তবে বিস্তার করেছে তার আধিপত্য। উত্তাল, সরোষ সমুদ্র নদীকে সেতু-শৃঙ্খলে করেছে বন্দী। সেই উচ্ছ্বসিত জল-প্রবহাকে মানুষ ব্যবহার করেছে তারই প্রয়োজনে। উষর ভূমিকে করেছে শস্যময়ী। মরুপ্রান্তরে এনেছে শ্যামল প্রাণের শিহরণ। ভূগর্ভের খনি থেকে তুলে এনেছে অজস্র সম্পদ। যানবাহনের আবিষ্কার দূরের ব্যবধান ঘুচিয়েছে। বিদ্যুৎ হয়েছে মানুষের পরম সুহৃদ, হয়েছে আধুনিক সভ্যতার অন্যতম শর্ত। কলকারখানা গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শহর-বন্দর। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে দূর দূরান্তের খবর পৌঁছে যায় মুহূর্তের মধ্যে। প্রয়োজনে সাহায্য চলে আসে দ্রুত। সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণ স্পর্শেই কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, মাঠে-প্রান্তরে সবুজ বিপ্লবের সফলতা। জীবনযাপনে এসেছে নিশ্চয়তা। বিজ্ঞানের সঞ্জীবনী মন্ত্রেই কমেছে অকাল মৃত্যুর হার। রোগ মহামারী বশ মেনেছে মানুষের কাছে।
বিজ্ঞানের অভিশাপঃ
বিজ্ঞানের এই অসীম জয়যাত্রায় মানুষ আরও এক অসীম শক্তির অধিকারী হলো। মানুষ আবিষ্কার করল পরমাণু শক্তির রহস্য। এই অনন্ত শক্তিকে যেমন একদিন মানুষ বৃহৎ কল্যাণে প্রয়োগ করল, তেমনি ধ্বংস সাধনেও যে এর ক্ষমতা অপরিসীম, তারও সন্ধান পেল মানুষ। পরমাণশক্তি পরিণত হলো আধুনিক সমরাস্ত্রে। বিজ্ঞানের কল্যাণপ্রসু আবিষ্কারই মানুষের অশুভ বুদ্ধির ফলে রূপান্তরিত হলো নির্মম অভিশাপে। পরমাণশক্তির ধ্বংসক্রিয়ার ভয়াবহতা প্রথম প্রমাণিত হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। বোমার। এই বোমার বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎসবে হাজার হাজার মানুষ ভস্মীভূত হয়ে গেল। প্রাণচঞ্চল শহর পরিণত হলো মহাশ্মশানে। জার্মানিতে হিটলারের নিষ্ঠুর গ্যাস-চেম্বারে নিহত হয়েছিল কত ইহুদি। বিজ্ঞানের এই মহাধ্বংসের ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করে মানুষ শিহরিত হলো। এখানেও এর ধ্বংস-উল্লাস থেমে থাকল না। দের আরও প্যন্ত মত্ততা, বিভীষিকা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল চীন কোরিয়া ভিয়েৎনাম আরব ভূখণ্ডের রণাঙ্গনে। বিজ্ঞান এর মধ্যে মানুষের হাতে তুলে দিল আরও নতুন নতুন মারণাস্ত্র। সে অস্ত্রের তালিকায় আরও একটি নাম, রাসায়নিক অস্ত্র। এই অস্ত্রের নৃশংসতা অকল্পনীয়। তাই, যে বিজ্ঞান একদিন ছিল মানুষের কাছে দেবতার আশীর্বাদের মত, আজ সেই বিজ্ঞানকেই মানুষ পরিণত করেছে মহাধ্বংসের মহাস্ত্রে। পরমাণুশক্তির অধিকারী দেশগুলো এখন আরও এক অশুভ অস্ত্র প্রতিযোগিতার খেলায় মেতেছে। আর সেজন্যেই মানুষ এমন আতঙ্কিত।
যান্ত্রিকতার অভিশাপঃ
বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের হাতে দিয়েছে অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। জীবনযাত্রার আদল গেছে বদলে। বেড়ে গেছে প্রয়োজনের সীমানা। যন্ত্রের অসীম ক্ষমতায় মানুষ পেয়েছে ভোগ-বিলাসের নানা উপকরণ। একদিন যন্ত্রের ওপর ছিল মানুষের আধিপত্য। আজ মানুষের ওপরই যন্ত্রের প্রভুত্ব। যন্ত্র ধীরে ধীরে মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে অবকাশ। তাকে দিয়েছে গতির আনন্দ। নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতা ক্রমশই মানুষকে আচ্ছন্ন করছে। বিনষ্ট করছে হৃদয়বৃত্তির অনুকূল উন্মেষ-পরিবেশকে। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতা গ্রাস করছে মানুষকে। যন্ত্রসভ্যতার কৃত্রিমতায় ঘটছে মানবতাবোধের অপমৃত্যু। কৃত্রিম জীবনযাপন হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতার অভিশাপ। এই যন্ত্র-যুগ মানুষকে আজ পরিণত করেছে যন্ত্রে। শিল্প-সাহিত্যেও সেই কৃত্রিমতারই প্রতিধ্বনি। এ-ও অগ্রগতির ছদ্মবেশে বিজ্ঞানেরই আর এক অভিশাপের চিত্র।
উপসংহারঃ
আজ বিজ্ঞানের সংহারমূর্তি দেখে, তার সর্বগ্রাসী যান্ত্রিকতার নিষ্প্রাণতা উপলব্ধি করে মানুষ যদি বিজ্ঞানকেই অভিশাপের কলঙ্কে চিহ্নিত করে, তবে সে দোষ বিজ্ঞানের নয়। দোষ মানুষের। মানুষের কল্যাণেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার, আর মানুষই সে-বিজ্ঞানকে পরিণত করেছে ধ্বংসের হাতিয়ারে। মানুষ নিধনই পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বার্থপর যুদ্ধবাজ প্রভুত্বকামী মানুষ লোভের প্রমত্ততায় অশুভ দানবীয় শক্তি নিয়ে মানুষের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত। আজও বিশ্বযুদ্ধের রণ-হুংকার দিকে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ আতঙ্কিত হয়। কেননা, পরমাণু যুদ্ধই হবে পৃথিবীতে শেষ যুদ্ধ। বিকৃত-বিলাসে কল্যাণপ্রস বিজ্ঞান পরিণত হয় ধ্বংসের অভিশাপে। কিন্তু মানুষেরই অন্তরে পাতা আছে মঙ্গলের দেবতার আসন। সেখানে তিনি চিরজাগ্রত প্রহরী।
…… এখানে আরো প্রবন্ধ রচনা যুক্ত করা হবে।